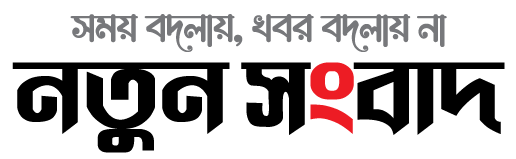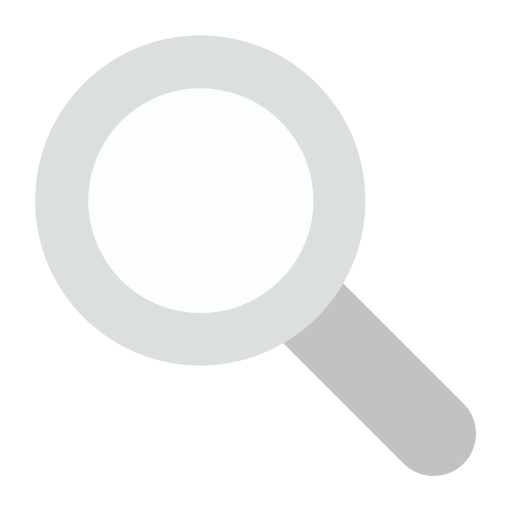এইচএসসি ফলাফলে সর্বনিম্ন পাসের হারে উন্মোচিত হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার গভীর সমস্যা। শিক্ষার মূল কাঠামোতে পরিবর্তন না এলে অগ্রগতি অসম্ভব।
গত ১৬ অক্টোবর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবারের ফলাফল দেখে ধাক্কা খেয়েছেন অনেকে। দেখা যাচ্ছে বিগত একুশ বছরের মধ্যে এবারই পাসে হার সর্বনিম্ন। ২০০৫ সালে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পাসে হার ছিল ৫৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। আর এবার ৫৭ দশমিক ১২ শতাংশ। মাঝের বছরগুলোতে পাসের হার ৬৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে।
এবার মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৭৫ দশমিক ৬১ শতাংশ আর কারিগরি বোর্ডে ৬২ দশমিক ৬৭ শতাংশ। সব বোর্ডের গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত বছর যা ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ।
ফলাফলের যে চারটি মূল সূচক রয়েছে, সবগুলোই এবার নিম্নমুখী। পাসের হার কমার পাশাপাশি জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যাও কমেছে। শতভাগ পাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, সব বোর্ডের মোট ১২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৬১ জন পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু পাস করতে পারেনি ৫ লাখ ৯ হাজার ৭০১ জন। গত বছর জিপিএ-৫ যেখানে পেয়েছিল এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন এবার সেখানে পেয়েছে মাত্র ৬৯ হাজার ৯৭ জন। শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠান গত বছর ছিল এক হাজার ৩৮৮টি, এ বছর মাত্র ৩৪৫টি। শূন্য পাস প্রতিষ্ঠান গতবছর যেখানে ছিল মাত্র ৬৫টি, এ বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০২টিতে।
শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এটাই প্রকৃত চিত্র। শিক্ষার্থীরা যা লিখেছে, তার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হয়েছে—কোনো বাড়িয়ে-কমিয়ে নয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবিরও একই কথা বলেন। তিনি এই ফলকে ‘বাস্তবতা’ বলে অভিহিত করে বলেন, “এই বাস্তবতাটা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। আমরা এই বাস্তবতাটা ফ্যাব্রিকেট করিনি।”
যদি তাদের বক্তব্য সঠিক হয়, তাহলে গত বছরগুলোতে ফলাফল ম্যানিপুলেট করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন তুগলকী কাণ্ড দীর্ঘদিন ধরে চলছে। সি আর আবরার হয়তো মনে করেছেন, খাতা মূল্যায়ন উদারভাবে হচ্ছিল, এখন কড়া করে দিতে হবে। কিন্তু আগামী বছর নতুন উপদেষ্টা এলে যদি আবার উদার করা হয়, তাহলে পাসের হার আবার বাড়বে—এই চক্রই চলছে।
শিক্ষা বিটে কয়েক বছর রিপোর্টার হিসেবে কাজ করার সুবাদে কিছু প্রবণতা লক্ষ করেছি। ২০০৮ সালে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের আমলে চট্টগ্রাম বোর্ড সবচেয়ে ভালো ফল করে, যা তার নিজের জেলার সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। পরে সিলেট অঞ্চলের এক সন্তান শিক্ষামন্ত্রী হলে সিলেট বোর্ড শীর্ষে চলে আসে। তারও আগে ১৯৯৩ সালের দিকে বাম্পার ফল হয় ৫০০ নম্বরের প্রশ্ন ব্যাংক নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বদৌলতে।
ফলাফলের ভালো-মন্দের মাপকাঠি আগের বছরের তুলনায় করা হয়, কিন্তু কেন এমন হয়েছে তা গবেষণার মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা হয় না। বেশি পাস দেখানোর মতো ফেল রাখারও কোনো গৌরব নেই। শিক্ষার্থী শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেও যথেষ্ট শিক্ষা পায় কিনা, না পেলে দায় কার—শিক্ষার্থী, পরিবার, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থা না রাষ্ট্রের, তা খুঁজে বের করতে হয়। জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা দরকার, কিন্তু তা নেই।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা, প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা সকলেই শিক্ষক। অনেকে আশা করেছিলেন বাজেটে শিক্ষা অগ্রাধিকার পাবে, কিন্তু পায়নি। শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে এখন উপদেষ্টা যা বলবেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে?
এবারের ফলাফল শিক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহ দিকটি তুলে ধরেছে। ঢাকা মহানগরীতে পাসের হার ৮৪ শতাংশ, কিন্তু একই বোর্ডের শরীয়তপুর-গোপালগঞ্জে ৪২ শতাংশ। টাঙ্গাইলে ৪৪, নরসিংদীতে ৬৮ শতাংশ। চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৭১, জেলায় ৪৪ শতাংশ। রাজশাহী মহানগরীতে ৯০, কিন্তু পুঠিয়ার পঞ্চমাড়িয়া কলেজে ২৫.১৫ শতাংশ। এতে শিক্ষায় চরম বৈষম্য স্পষ্ট হয়েছে। ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন, সচ্ছল এলাকায় ফল ভালো হয়।
তবে কিছু চমকপ্রদ তথ্যও আছে। ঢাকার নটরডেম কলেজে ৩,২৩৯ জনের মধ্যে ৯৯.৬০ শতাংশ পাস, ২,৪৫৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে—যা অনেক শিক্ষা বোর্ডের চেয়েও বেশি। ক্যাডেট কলেজগুলোতে ৫৮৯ জনের মধ্যে ৫৮৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এসব দেখায়, ভালো করার উদাহরণ দেশেই আছে।
যারা ফেল করেছে আমরা তাদের নিয়েই কথা বলছি। ১২ লাখের বেশি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখের বেশি ফেল, আর ১২ বছর আগে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ঝরে পড়া আরও ১২ লাখের কথাও ভাবতে হবে। ভাবতে হবে শিক্ষার আওতায় না আসা শিশুদেরও কথা।
এই অবস্থায় পাস-ফেল করানোর মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব নয়। অগ্রগতির জন্য প্রসার ও মানোন্নয়ন, স্থির লক্ষ্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে মন দিতে হবে।
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখন কোন পর্যায়ে আছে এক নজরে দেখে নিতে পারি।
দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এখন ব্যবসার মতো হয়ে উঠেছে। যেখানে চলছে, সেখানে অনুরূপ আরও গড়ে উঠছে—কেজি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। জাতীয় চাহিদা অনুসারে কোথায় কী প্রয়োজন, তার কোনো গাইডলাইন নেই।
সময়োপযোগী বিষয় পড়ানোর জন্য কোনো গবেষণা বা কর্তৃপক্ষ নেই। এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে, বেশিরভাগেরই জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শিক্ষক নেই, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও নেই। ২০১৭ সালে গঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এখনও নিষ্ক্রিয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) শুধু বই ছাপায়, গবেষণা করে না।
ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদের পেছনে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যে সব পরিবার তার শিক্ষার্থীকে দশটি বিষয়ের দশটি কোচিংয়ে পড়িয়েছে কিংবা একজন শিক্ষার্থীর পেছনে দশজন প্রাইভেট টিউটর লাগিয়ে দিতে পেরেছে তারা ভালো ফল করেছে। কিন্তু এমন সামর্থ্য কত পরিবারের আছে? ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো সিস্টেম তৈরি করে হোমওয়ার্ক দিয়ে চালায়, ক্লাসে শিক্ষা হয় না। গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে তো এমনও হয় না, শিক্ষকদের দক্ষতা-প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান-দক্ষতা থেকে বঞ্চিত। এ কারণেই সদ্যপ্রয়াত শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম চৌধুরী দুঃখ করে বলেছিলেন, “আমরা শিক্ষার্থী নয়, পরীক্ষার্থী তৈরি করছি”।
শিক্ষার লক্ষ্য কী? সেটা কি পরিস্কার? না। একসময় কেরানি তৈরির জন্য শিক্ষা শুরু হয়েছিল, ‘বাবু তৈরি’র ওই শিক্ষা থেকে বের হতে পেরেছি কি? লক্ষ্য কি শিক্ষিত, মননশীল, জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠন নাকি দক্ষ জনশক্তি তৈরি? না দুটোই? কিছুই তো পরিষ্কার না।
৫০-৬০-এর দশকে ভাষা আন্দোলনের পর ছাত্ররা শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন করে। তারপর শিক্ষা রাজনীতিতে ইস্যু হয়নি। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ, ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক ঘোষণা, নুরুল ইসলাম নাহিদের আমলে বিনামূল্যে বই—কিন্তু অগ্রগতি আটকে আছে এতেই। ৫৬ বছরেও প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হয়নি, কর্মমুখী শিক্ষাও প্রসারিত হয়নি। ২০১০ সালের টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি অর্থের অভাবে। এসবরে মাধ্যমে অগ্রাধিকারের সংকটটিই সামনে চলে আসে।
শিক্ষায় অগ্রাধিকার না দিয়ে কোনো জাতি এগোয়নি। ইউনেসকোর পরামর্শে জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করতে হয়, কিন্তু আমরা করছি ২ শতাংশের নিচে। দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম। যুক্তরাষ্ট্রের এক জরিপে দেখা গেছে, ১ ডলার শিক্ষায় বিনিয়োগে অর্থনীতিতে ৮ ডলার যোগ হয়। কিন্তু আমরা উপেক্ষা করছি শিক্ষায় বরাদ্দের প্রসঙ্গটিকে। এ ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও অদ্ভুত মিল রয়েছে। শিক্ষায় বরাদ্দের ক্ষেত্রে এক দল আরেক দলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কখনোই করে না।
সমাজের অধঃপতনও শিক্ষায় প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষকদের মর্যাদা নেই। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নানাভাবে শিক্ষকদের হেনস্থা করাটা চোখে পড়েছে। শিক্ষককে গুরুত্ব না দিলে শিক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হয় না। এই মুহূর্তে ছয় লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক শহীদ মিনারে আন্দোলন করছেন। তাদের বাসাভাড়া দেওয়া হয় মাত্র এক হাজার টাকা! শিক্ষকদের বাসা ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর মতো যৌক্তিক দাবি অর্থের অজুহাতে মানা হচ্ছে না, কিন্তু কর্মকর্তাদের গাড়ির ভাতা ৫০,০০০ টাকায় সমস্যা নেই। শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়াতে হবে, পর্যাপ্ত বেতন-প্রশিক্ষণ দিয়ে মেধাবীদের আকর্ষণ করতে হবে।
স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের বিষয়টি আলোচনায় আসে মাঝে মধ্যেই। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার যারা সারা বছরই শিক্ষা নিয়ে কাজ করবে, গবেষণা করবে। সরকার তাদের মতামত যাচাই বাছাই করে তা প্রয়োগ করবে।
শিক্ষা নিয়ে গবেষণায় জোর দিতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নের কাজে বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কারা—এ নিয়েও রয়েছে ভ্রান্তি। চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে না পড়লে চিকিৎসাবিদ হওয়া যায় না, ইতিহাস নিয়ে না পড়লে ইতিহাসবিদ বলা হয় না। কিন্তু যে কোনো বিখ্যাত শিক্ষিতজনকেই শিক্ষাবিদ বলতে দেখি। সবার সব বিষয়ে বক্তব্য থাকতে পারে কিন্তু নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষাগবেষক ও প্রকৃত শিক্ষাবিদদেরই গুরুত্ব দিতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা নিয়ে পড়ালেখা, গবেষণা করা লোক দেশে নেহায়েত কম নয়। তাদের কাজে লাগতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।