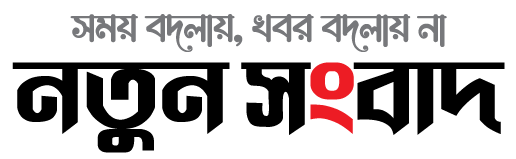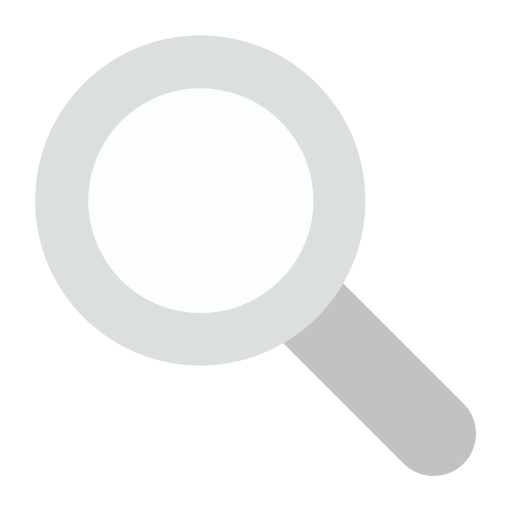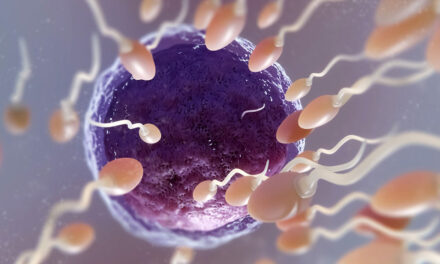বেশিরভাগ যাত্রীবাহী প্লেন সাধারণত মাক ০.৮, মানে শব্দের গতির চেয়ে কিছুটা ধীরে ওড়ে। কারণ এর চেয়ে বেশি গতি মানেই বেশি সমস্যা আর বেশি জ্বালানি খরচ।

হতে সংগৃহীত
২০০৩ সালে ডানা গুটিয়ে নিতে হয়েছিল বিশ্বের প্রথম সুপারসনিক যাত্রীবাহী জেট কনকর্ডকে। এরপর চলে গেছে দুই দশকের বেশি সময়।
এতদিন পর শব্দের চেয়েও দ্রুত উড়ার সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এক যাত্রীবাহী জেটের প্রোটোটাইপ।
এ বছরের শুরুতে ‘এক্সবি ১’ নামের জেটের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে বিশ্বের দ্রুতগতির উড়োজাহাজ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করা মার্কিন স্টার্টআপ ‘বুম সুপারসনিক’।
বুম সুপারসনিকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ব্লেক শোল ২০২২ সালে গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন, কনকর্ড যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে সফল হবে তার কোম্পানি। কারণ, কনকর্ডের চেয়ে হালকা ও আরও সক্ষম হবে তাদের বিভিন্ন জেট।
কিন্তু একটি যাত্রীবাহী প্লেন সুপারসনিক গতিতে পৌঁছালে তখন আসলে কী ঘটে?
সুপারসনিক গতিতে পৌঁছালে যা ঘটে
যাত্রীবাহী কোনো প্লেনের গতি যখন এক মাক পেরিয়ে যায় বা শব্দের চেয়ে বেশি হয়, তখন প্লেনে এক শকওয়েভ তৈরি হয়। এ সময় প্লেনের ওপর বায়ুর টান বা ড্র্যাগ হঠাৎ করেই বেড়ে যায় ও ইঞ্জিনকে বেশি জ্বালানি পোড়াতে হয় বলে প্রতিবেদনে লিখেছে প্রযুক্তি বিষয়ক সাইট স্ল্যাশগিয়ার।
এ সময় ভূমিতে থাকা মানুষজন বিস্ফোরণের মতো তীব্র আওয়াজ শব্দ শুনতে পান, যাকে বলা হয় ‘সনিক বুম’। এ শব্দ যেন আকাশ থেকে ভেঙে পড়া বজ্রপাতের মতো শোনায় এবং তা এড়ানো সম্ভব নয়।
১৯৭০-এর দশকে কনকর্ড সুপারসনিক যাত্রীবাহী প্লেনকে এ একই সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। বর্তমান যুগের বিভিন্ন আধুনিক সুপারসনিক জেটও ঠিক একই রকম পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য।
এ উচ্চ গতিতে মাক ১ বা তার ওপরে উড়তে হলে প্লেনের ডানার ও দেহের ডিজাইন এমনভাবে তৈরি করতে হয়, যাতে প্লেনে বাতাসের ঘর্ষণ বেড়ে অতিরিক্ত গরম না হয়। পাশাপাশি উচ্চ গতিতে উড়লে প্লেনের বাতাস কেটে যাওয়ার সক্ষমতাও কমে যায়।

এ বছরের শুরুতে ‘এক্সবি ১’ নামের জেটের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে মার্কিন স্টার্টআপ ‘বুম সুপারসনিক’। ছবি: বুম সুপারসনিক
ফলে বেশিরভাগ যাত্রীবাহী প্লেন সাধারণত মাক ০.৮, মানে শব্দের চেয়ে কিছুটা ধীর গতিতে ওড়ে। কারণ এর চেয়ে বেশি গতি মানেই বেশি সমস্যা আর বেশি জ্বালানি খরচ।
আজকের বুম সুপারসনিকের ‘এক্সবি ১’ জেটের প্রোটোটাইপ থেকে প্রমাণ মিলেছে, এ প্রযুক্তি এখনও কার্যকর। পরীক্ষার সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার আকাশে প্রায় ৩৫ হাজার ফিট উচ্চতায় জেটটি মাক ১.১২ গতিবেগে বা ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার তিনশ ৬০ কিমি গতিতে যাত্রা করেছে। বাতাসে শব্দের গতি ঘণ্টায় এক হাজার দুইশ ৩৪ কিলোমিটার।
এ পরীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে, ছোট বিভিন্ন জেট প্লেন নিরাপদভাবে শব্দের গতি পেরিয়ে যেতে পারে। তবে এ প্রযুক্তিকে বড় পরিসরে যাত্রী পরিবহনের উপযোগী করে তোলা, যেমন– বুম সুপারসনিক তাদের ৬৫ আসনের ওভারচার প্লেন দিয়ে যদি এমনটি করতে চায় তবে সেখানে আসল চ্যালেঞ্জ শুরু হয়।
জ্বালানি পোড়ানো এবং জলবায়ু প্রভাব
সুপারসনিকে যাত্রার অনিবার্য সমস্যা হচ্ছে এর সক্ষমতা। শব্দের গতি ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় বায়ুর বাধা বা ড্র্যাগ ঠেকাতে এসব জেটকে প্রতি যাত্রীর জন্য আজকের সাবসোনিক বা সাধারণ গতির প্লেনের চেয়ে দুই থেকে তিন গুণ বেশি জ্বালানি পোড়াতে হয়। ফলে এতে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও ব্ল্যাক কার্বন নির্গত হয়, যা প্রায়ই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে এসব দূষক পদার্থ দীর্ঘ সময় ধরে থাকে ও বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষতি করে।
তবে বুম সুপারসনিকের দাবি, তাদের ওভারচার প্লেন একশ ভাগ টেকসই জ্বালানি ব্যবহার করবে। এর বড় সীমাবদ্ধতাও আছে। এই টেকসই জ্বালানির জোগান খুবই কম এবং দাম অনেক বেশি। আর, সুবিধা হচ্ছে, সাধারণ জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় কার্বন নিঃসরণ ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে।
এ ছাড়া টেকসই প্লেন জ্বালানিতে সালফারের পরিমাণ কম থাকায় প্লেনটি যদি ৬০ হাজার ফুট উচ্চতায়, যেখানে একসময় কনকর্ড উড়ত সেই উচ্চতায় পোড়ানো হয় তবে তা বায়ুমণ্ডলকে উল্টো আরও বেশি উষ্ণ করতে পারে।
সুপারসনিক বিভিন্ন প্লেন আকাশে সেই সাদা রেখা তৈরি নাও করতে পারে, কারণ এরা বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে ওড়ে, সেখানে বাতাস অনেক বেশি শুকনো থাকে, যা পরিবেশের জন্য ভালো বিষয়। বর্তমানে উড়োজাহাজ পরিবহন খাতের ওপর নির্গমন কমানোর জন্য বড় চাপ রয়েছে। গোটা বিশ্ব চাচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ‘শূন্যে’ নামিয়ে আনতে। তবে সুপারসনিক প্লেন চালু করা এ লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করবে, কারণ এগুলো পরিবেশবান্ধব নয়।