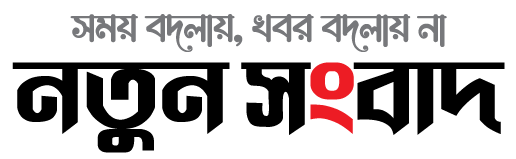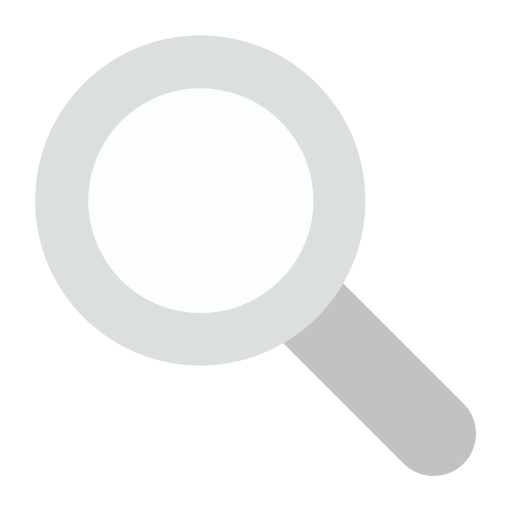দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একের পর এক গণ-অভ্যুত্থান দেখা গেছে। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার আরাগালয় (জনতার সংগ্রাম) আন্দোলন একজন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেয়।
২০২৪ সালে বাংলাদেশে ছাত্র জনতার আন্দোলন কয়েক দশকের কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটায়। পাকিস্তান রাস্তায় সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে টলতে থাকে। আর এবার পালা নেপালের।
হিমালয়ান প্রজাতন্ত্র নেপাল কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অস্থিরতার মুখে পড়েছে। কাঠমান্ডু ও অন্যান্য বড় শহরে ছড়িয়ে পড়েছে প্রবল বিক্ষোভের ঝড়। এর নেতৃত্ব দিচ্ছে তরুণ প্রজন্ম, বিশেষত জেনারেশন জেড বা জেন-জি।
দুর্নীতি, ব্যর্থ শাসন এবং হঠাৎ করে ডিজিটাল স্বাধীনতার ওপর হামলার মিশ্রণ এই আন্দোলনের জ্বালানি। সেখানে এ পর্যন্ত ১৯ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে শত শত মানুষ। সেনাবাহিনী এখন রাস্তায়।
ধারণা করা হচ্ছে, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে। শিক্ষার্থীরা ব্যারিকেড ভাঙছে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াচ্ছে। এমনকি সংসদ ভবনের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে।
এসব দৃশ্য পুরো অঞ্চলকে নাড়া দিয়েছে। নেপাল নামের যে দেশটিকে বাইরে থেকে অনেকেই শান্ত একটি পর্যটন স্বর্গ বলে ভাবেন, আজ সে দেশ গণবিপ্লবের ময়দানে পরিণত হয়েছে।
এই অস্থিরতার স্ফুলিঙ্গ ছিল সরকারের একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তটি হলো দুই ডজনেরও বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া।
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব আর এক্স (আগের টুইটার) এক রাতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবল টিকটক টিকে ছিল, কারণ তারা সরকারের নিবন্ধন নীতি মেনে নিয়েছিল। সরকারের ব্যাখ্যা ছিল—বিধি লঙ্ঘন, ঘৃণামূলক বক্তব্য ও অনলাইন অপব্যবহারের কারণে এগুলো বন্ধ করা হয়েছে।
কিন্তু তরুণ নেপালিদের কাছে এটি ছিল স্রেফ সেন্সরশিপ। তাঁরা এটিকে নিজেদের মতপ্রকাশ, সংগঠন গড়ে তোলা এবং ডিজিটাল যুগে বেঁচে থাকার অধিকারের ওপর আঘাত হিসেবে দেখেছেন।
শুরুতে নির্দিষ্ট স্থানে সমাবেশ হলেও দ্রুত তা গণমিছিলে রূপ নেয়। এটি ছড়িয়ে পড়ে কাঠমান্ডু, পোখারা, বিরাটনগর ও ভরতপুরে। আন্দোলনকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেন। সরকারি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। এমনকি সংসদ ভবনও আক্রান্ত হয়।
কঠোর দমননীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র এসবের জবাব দিয়েছে। রাস্তায় গুলি ছোড়া হয়েছে। রাবার বুলেট আর টিয়ারগ্যাসে বাতাস ভরে গেছে। লাঠিপেটায় বহু মানুষ রক্তাক্ত হয়েছে।
সরকারি বাহিনীর ধরপাকড়ের পর হাসপাতালে শয্যা ফুরিয়ে গিয়েছিল, কারণ আহতদের ভিড় সামলানো যাচ্ছিল না। কারফিউ আর রাস্তা অবরোধে এখনো পাড়া-মহল্লা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে সেনা নামানো হয়েছে।
তবুও প্রতিবাদ থামেনি। বরং তা আরও বড় হয়েছে। আরও ক্ষুব্ধ হয়েছে—যেন তরুণ প্রজন্ম বিশ্বাস করে বসেছে, সরকার কেবল ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার জন্যই তাদের ওপর দমন চালাচ্ছে। যা শুরু হয়েছিল ডিজিটাল অধিকারের দাবিতে, তা দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।
ক্ষমতাসীন অভিজাতরা ভেবেছিলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করলেই বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তার উল্টোটা হয়েছে। এটাই তরুণদের জন্য হয়ে উঠেছে স্লোগান ও সংগ্রামের ডাক।
‘দুর্নীতি বন্ধ করো, সামাজিক মাধ্যম নয়’—এটিই এখন আন্দোলনের মূল স্লোগান। এটি প্রকৃত ক্ষতকে সামনে এনেছে। সেই ক্ষতটি হলো, দশকের পর দশক ধরে নেপালের রাজনীতিকে গ্রাস করা দুর্নীতি আর দায়মুক্তির সংস্কৃতি।
নেপালের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই অস্থিতিশীলতা ও কেলেঙ্কারিতে ভরা। সরকার গড়া ও ভাঙা যেন এক অন্তহীন খেলা। জোট ভেঙে যায় তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। নেতারা সহজেই দলবদল করেন। কিন্তু যে জিনিস কখনো বদলায় না, তা হলো দুর্নীতির কালো ছায়া।
পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই একটা স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কায়, বাংলাদেশে, আর এখন নেপালে—তরুণ প্রজন্মই ব্যর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। যে সামাজিক মাধ্যমকে একসময় তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া হতো, সেটাই হয়ে উঠেছে সংগঠন, দুর্নীতি ফাঁস আর বিদ্রোহের হাতিয়ার।
শুধু ২০২৫ সালেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রী ঘুষের অভিযোগে পদত্যাগ করেছেন। এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হয়েছেন।
বিমানবন্দর নির্মাণে জালিয়াতি, নেপাল টেলিকমে অর্থ আত্মসাৎ, অভিবাসন দপ্তরে চাঁদাবাজি—এসব কেলেঙ্কারিতে রীতিমতো তোলপাড় হয়েছে। স্বর্ণ চোরাচালান ও শরণার্থী প্রতারণা কেলেঙ্কারিতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সাধারণ মানুষ দেখেছে, বড় নেতাদের আসলে কোনো সাজা হয় না। সেখানে দেখা যায়, তদন্ত দীর্ঘায়িত হয়, নিচুতলার কর্মীরা শাস্তি পান, অথচ ক্ষমতাবানরা বেঁচে যান।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাজনীতিকদের সন্তানদের বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের পোশাক-গয়না প্রদর্শনের ছবি ভাইরাল হয়েছে। তাঁদের ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে—‘নেপো কিডস’। #NepoKids এবং #PoliticiansNepoBabyNepal হ্যাশট্যাগ সেখানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
একটি তীব্র তুলনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে—‘তাদের সন্তানরা গুচির ব্যাগ নিয়ে ফেরে, আমাদের সন্তানরা কফিনে ফেরে।’
এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয় সেই বাস্তবতা: নেতাদের সন্তানরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরে দামি পণ্যের ঝাঁপি নিয়ে, আর সাধারণ পরিবারের সন্তানরা অসুরক্ষিত প্রবাসী শ্রমের শিকার হয়ে উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে কফিনে লাশ হয়ে ফেরে।
এই দায়মুক্তির সংস্কৃতি জনআস্থাকে ভেঙে চুরমার করেছে। অর্থনীতি তীব্র ধাক্কা খেয়েছে। নেপালিরা কর দেন, কিন্তু এর বিনিময়ে সড়ক, হাসপাতাল, স্কুলের উন্নতি পান না। মন্ত্রীরা কেবল নিজেদের পকেট ভারী করেন।
তাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বন্ধ হওয়া কেবল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার ঘটনা নয়, এটি জনগণের চোখে ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত শ্রেণির অপরাধ ঢাকার নতুন কৌশল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমই ছিল সেই মঞ্চ, যেখানে তরুণেরা নেতাদের বিরুদ্ধে ‘ডিজিটাল ট্রায়াল’ চালাতেন। মিম, ভিডিও ও ভাইরাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দুর্নীতি ফাঁস করতেন।
এই প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করার পদক্ষেপ ছিল যেন সেই নৈতিক জবাবদিহিকে শ্বাসরোধ করে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা।

এই আন্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছে জেন-জি। নেপালে এটাই সবচেয়ে বড় জনসংখ্যার গোষ্ঠী। এ প্রজন্ম বড় হয়েছে স্মার্টফোন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং বৈশ্বিক সংযোগের ভেতর দিয়ে।
কিন্তু তাঁদের অনেকেই দেশে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পর্যটন ও সেবা খাতের সংকুচিত সুযোগের মধ্যে তাঁরা আটকে আছেন অথবা বাধ্য হচ্ছেন অনিশ্চিত গিগ অর্থনীতির কাজে যুক্ত হতে। অন্যরা দেশ ছাড়ছেন, যোগ দিচ্ছেন সেই প্রবাসী শ্রমিকদের দলে, যাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স নেপালের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।
এই রকম একটা সময়ে জেন-জি সেই হতাশাকে আন্দোলনে রূপ দিল। তাঁরা মিম, হ্যাশট্যাগ আর নাটুকা স্কিট ব্যবহার করে দুর্নীতিকে তুলে ধরলেন এক প্রজন্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে।
তাঁরা এনক্রিপটেড চ্যাট আর অফলাইন নেটওয়ার্কে মিছিল সংগঠিত করলেন। আন্দোলনে দেখা গেল এমন সব প্ল্যাকার্ড, যেগুলো সরাসরি ভাইরাল পোস্ট থেকে অনুপ্রাণিত। অনলাইন আর অফলাইনের সীমারেখা একেবারে ঝাপসা হয়ে গেল। যে প্ল্যাটফর্মগুলো আগে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের জায়গা ছিল, তার সম্প্রসারণ হয়ে উঠল রাজপথ।
এই আন্দোলন ছিল নেতাবিহীন। কোনো দল বা ব্যক্তি এর মালিকানা দাবি করতে পারেনি। এটা ছিল সচেতন কৌশল। নেপালে রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্নীতি আর সুযোগসন্ধানীর প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। তাই দলীয় সীমারেখা প্রত্যাখ্যান করে তরুণেরা তৈরি করল এক বিবেক-নির্ভর আন্দোলন। সেই আন্দোলনের মূল বক্তব্য হলো—‘ক্ষমতা দখলের জন্য নয়’।
তাঁরা কৌশল আর অনুপ্রেরণা নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের জেন-জি আন্দোলন থেকে, যেখানে যুবকেরা প্রতিষ্ঠিত অভিজাতদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। নেপালে এই আন্দোলন নীতি বা নীতিমালার চেয়েও বেশি মর্যাদার প্রশ্নে দাঁড়িয়েছে। এটা মূলত এক রাষ্ট্রের কাছে সম্মান দাবি, যে রাষ্ট্র তাঁদের সব সময় অবাধ্য শিশু হিসেবে দেখেছে।
তবে ঝুঁকিও আছে।
বিনিয়োগকারীদের আস্থা ইতিমধ্যেই টলে গেছে। নেপালের প্রাণরেখাখ্যাত পর্যটন খাত হুমকির মুখে। প্রবাসী রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলো অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। ভারতও শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কারণ ইতিহাসে দেখা গেছে, নেপালের অস্থিরতা অনেক সময় সীমান্ত ছাপিয়ে যায়। শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের প্রতিধ্বনি এখানে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ‘ডিজিটাল ট্রায়াল’ অনেক সময় পক্ষপাত আর ভুয়া তথ্য ছড়ায়। আর রাগ-ক্ষোভ যে বাস্তব সংস্কারে রূপ নেবে তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু যা স্পষ্ট তা হলো—একটা পুরো প্রজন্ম আর নেতাদের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে না। তাঁরা নিজেরাই পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সরকার এখন এমন এক ঝড়ের কেন্দ্রে, যেটা তারা সামলাতে পারছে না। প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত উল্টো বিপর্যয় ডেকে এনেছে। দুর্নীতির কেলেঙ্কারি জনরোষকে আরও তীব্র করেছে।
সহিংস দমননীতিতে শিক্ষার্থীরা শহীদে পরিণত হয়েছে, প্রজন্মের বিভাজন আরও গভীর হয়েছে। ইতিমধ্যেই মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন। একের পর এক জরুরি কেবিনেট বৈঠক হচ্ছে। এমনকি উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতির মামলাগুলোতে দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিচার বিভাগও এখন তীব্র সমালোচনার মুখে।
অনেক নেপালির কাছে রাষ্ট্র আর তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছে না। রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে এক অভিজাত ক্লাব—যারা জবাবদিহির বাইরে, শোনার চেয়ে চুপ করিয়ে দেওয়াতেই বেশি আগ্রহী। এ কারণেই রাজতন্ত্রপন্থী সমাবেশ আবারও মাথা তুলছে।

সাংবিধানিক পরিবর্তনের দাবি ফিসফিস করে শোনা যাচ্ছে। ওলির সরকার কেবল কর্তৃত্বকে নয়, গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিটুকুকেও ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।
যদি দমননীতি চলতেই থাকে, তবে অস্থিরতা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে।
বিনিয়োগকারীদের আস্থা ইতিমধ্যেই টলে গেছে। নেপালের প্রাণরেখাখ্যাত পর্যটন খাত হুমকির মুখে। প্রবাসী রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলো অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। নেপালের এই আন্দোলনে ভারতও শঙ্কিত। কারণ ইতিহাসে দেখা গেছে, নেপালের অস্থিরতা অনেক সময় সীমান্ত ছাপিয়ে যায়। শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের প্রতিধ্বনি এখানে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।
মৃত্যুর সংখ্যা যত বাড়বে, নেপালের তরুণ আন্দোলন ততই তীব্র হবে। এটা নিঃসন্দেহে এক প্রজন্মের বিদ্রোহ—দুর্নীতি, বঞ্চনা আর দমননীতির বিরুদ্ধে। এ বিদ্রোহ শাসক শ্রেণিকে স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে—‘যে রাজনীতি এত দিন চলে আসছিল, তার অবসান হয়েছে।’
রাষ্ট্রের সামনে এখন দুটি পথ খোলা। হয় তারা নিষেধাজ্ঞা, গুলি আর ঘুষের নীতি আঁকড়ে ধরতে পারে যা কিনা তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভাঙবে। অথবা তারা সংলাপের দরজা খুলতে পারে, সেন্সরশিপ তুলে নিতে পারে, আর সত্যিকারের সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতির মোকাবিলা করতে পারে।
সরকার কোন পথ বেছে নেবে তার ওপরই নির্ভর করছে—২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর কেবল আরেকটি অস্থিরতার অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে লেখা থাকবে, নাকি এটি হবে নতুন রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের সূচনা।
পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই একটা স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কায়, বাংলাদেশে, আর এখন নেপালে—তরুণ প্রজন্মই ব্যর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। যে সামাজিক মাধ্যমকে একসময় তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া হতো, সেটাই হয়ে উঠেছে সংগঠন, দুর্নীতি ফাঁস আর বিদ্রোহের হাতিয়ার।
সরকারগুলো যখন একে বন্ধ করতে চেয়েছে, তখন তারা আবিষ্কার করেছে—দমননীতি কেবল বিদ্রোহকেই উসকে দেয়।
অঞ্চলের পুরোনো অভিজাত শ্রেণিকে এখন সতর্ক হতে হবে। তারা চাইলেই এই জোয়ার থামাতে পারবে না। নতুন প্রজন্ম ক্ষমতার দরজায় কড়া নাড়ছে—আর তারা চুপচাপ ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা রাখে না।
- কে. এম. সীথি মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কেরালা) ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড এক্সটেনশন (আইইউএসএসআরই)-এর পরিচালক
ইউরেশিয়া রিভিউ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ
সংগৃহীত