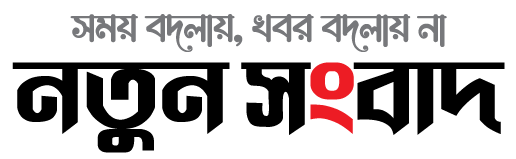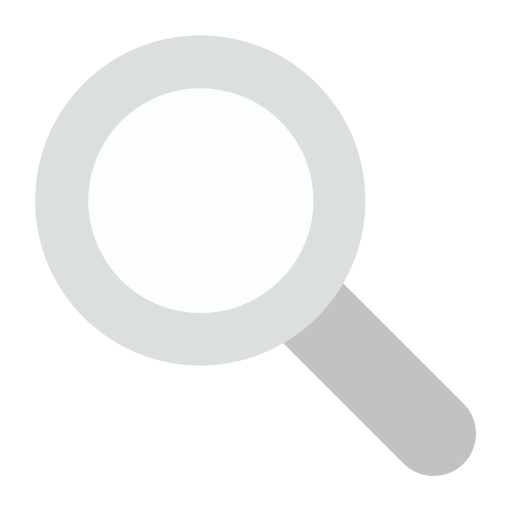লবণের স্ফটিক, যেগুলোকে ‘হ্যালাইট’ বা শিলালবণ বলা হয় এগুলো পানির স্তরের নিচে নেমে যাচ্ছে। বিষয়টি এমন যেন পানির নিচে ‘লবণের তুষারপাত’ হচ্ছে।

পৃথিবীর অন্যতম অদ্ভুত স্থানের মধ্যে একটি ডেড সি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভে লবণের স্তর জমে জমে কীভাবে লবণের পাহাড় গঠিত হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদেরকে নতুন ধারণা দিয়েছে পৃথিবী পৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু স্থানে থাকা ও অতিরিক্ত লবণাক্ততার জন্য পরিচিত এ গভীর লবণাক্ত হ্রদটি।
বিশাল আকারের এসব লবণের স্তর গঠনের পেছনের নানা প্রক্রিয়া নিয়ে নজর দিয়েছে ‘ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, সান্তা বারবারা’র অধ্যাপক একার্ট মাইবুর্গের নেতৃত্বে পরিচালিত এক সাম্প্রতিক গবেষণা।
লবণের এসব স্তর সাগরের গভীরে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ও এর পুরুত্ব এক কিলোমিটার বা তারও বেশি বলে প্রতিবেদনে লিখেছে বিজ্ঞানভিত্তিক সাইট নোরিজ।
গবেষকরা বলছেন, এসব স্তরকে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মতো জায়গার গভীরে লুকিয়ে থাকতে দেখা গেলেও ডেড সি এমন এক বিরল স্থান, যেখানে এখনও চোখের সামনে এগুলোর গঠন প্রক্রিয়ার দেখা মেলে।
ডেড সি’কে বিশেষ ধরনের এক গবেষণাগার হিসেবে গড়ে তুলেছে এর অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। এটি এক ধরনের লবণাক্ত পানির টার্মিনাল হ্রদ, অর্থাৎ এর কোনো বহির্গমন পথ নেই। তাই পানি কেবল বাষ্পীভবনের মাধ্যমে এখান থেকে বেরিয়ে আসে। আর পানি বাষ্প হয়ে উবে যাওয়ার সময় লবণ ফেলে রেখে যায়।
হাজার হাজার বছর ধরে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরু লবণের স্তর তৈরি হয়েছে ডেড সি’র গভীরে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের কর্মকাণ্ড, যেমন– ‘মৃত’ এ সাগরে পানি সরবরাহকারী জর্দান নদীর প্রবাহে বাঁধ দেওয়ার মতো বিভিন্ন কাজ এ প্রক্রিয়ার গতি বাড়িয়েছে।
গবেষকরা বলছেন, এখন ডেড সি’র পানির স্তর প্রতি বছর প্রায় এক মিটার করে কমে যাচ্ছে। ফলে আরও বেশি লবণ এর গভীরে জমছে এবং হ্রদের গঠনেও পরিবর্তন আনছে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে তাপমাত্রা। একসময় ‘মেরোমিকটিক’ ছিল ডেড সি, যেখানে সারা বছরজুড়ে এ সাগরের পানি স্তরে স্তরে বিভক্ত থাকত। উপরের স্তরে থাকত উষ্ণ ও তুলনামূলকভাবে কম লবণাক্ত পানি এবং নিচের স্তরে থাকত ঠান্ডা ও বেশি লবণাক্ত পানি। এই স্তরবিন্যাসের কারণে লবণ পুরো হ্রদের পানিতে সমানভাবে মিশে যেতে পারত না।
তবে ১৯৮০-এর দশকে যখন ডেড সি’তে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমে যায় তখন এর উপরিভাগের পানির লবণাক্ততা বেড়ে যায়। এতে সাগরের পানির বিভিন্ন স্তর মিশে যেতে শুরু করে ও ডেড সি ‘হোলোমিকটিক’ হ্রদে পরিণত হয়, যেখানে এখন এটি বছরে অন্তত একবার পুরোপুরি মিশে যায়।
এ মিশ্রণের পরেও উষ্ণ মাসে হ্রদ আবার স্তরে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ঠিক এই সময়ে হ্রদে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ২০১৯ সালে মাইবুর্গের এক গবেষণা দল আবিষ্কার করে, লবণের স্ফটিক, যেগুলোকে ‘হ্যালাইট’ বা শিলালবণ বলা হয় এগুলো পানির স্তরের নিচে নেমে যাচ্ছে। বিষয়টি এমন যেন পানির নিচে ‘লবণের তুষারপাত’ হচ্ছে।
গবেষকরা বলছেন, এটি বিস্ময়কর। কারণ, সাধারণত লবণ ঠান্ডা পরিবেশে বেশি স্ফটিক আকারে জমে। তবে গরমে বাষ্পীভবনের কারণে উপরের পানির লবণাক্ততা বেড়ে যায় ও উপরের উষ্ণ স্তর আরও বেশি লবণ দ্রবীভূত রাখতে পারে। এ কারণেই সেখানে ‘ডবল ডিফিউশন’ নামের এক বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়।
গরম ও লবণাক্ত পানি ঠান্ডা হয়ে নিচে নামে, আর তুলনামূলক ঠান্ডা পানি উপরে উঠে গরম হয়। যখন উপরের স্তর ঠান্ডা হয় তখন অতিরিক্ত লবণ স্ফটিক হিসেবে গঠিত হতে শুরু করে ও নিচে পড়ে যায়।
এ চলমান লবণের তুষারপাত, যা ঋতু পরিবর্তন, বাষ্পীভবন ও হ্রদের প্রবাহের সঙ্গে মিলে ঘটে ও এর মাধ্যমে লবণের বিভিন্ন বড় বড় স্তর ধীরে ধীরে কী ভাবে তৈরি হয় তার ব্যাখ্যা মিলেছে। বিজ্ঞানীদের জন্য এ এক বিরল সুযোগ, যেখানে এই ভূতাত্ত্বিক দৈত্যদের কার্যকলাপের দৃশ্য সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছেন তারা।
কোটি কোটি বছর আগে ভূমধ্যসাগরেও একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যা পৃথিবীর অন্যতম পুরু লবণের স্তর গঠনে সাহায্য করেছিল। ওই সময় ভূমধ্যসাগর শুকিয়ে গিয়েছিল, যাকে ‘মেসিনিয়ান স্যালিনিটি ক্রাইসিস’ বলা হয়। পরে জিব্রালটার প্রণালী আবার খুলে গেলে ভূমধ্যসাগর পুনরায় পানিতে ভরে যায় ও পুরু লবণের বিভিন্ন স্তর গভীরেই থেকে যায়।
ডেড সি’র পানির নিচের ঝর্ণা ও পরিবর্তিত লবণের বিভিন্ন স্তর অদ্ভুত আকৃতির লবণ চিমনি ও গম্বুজ তৈরিতেও সাহায্য করেছে বলে প্রতিবেদনে লিখেছে নোরিজ।
এসব প্রক্রিয়া গবেষণা করে কেবল প্রাচীন ভূতত্ত্বই নয়, বরং আধুনিক কিছু চ্যালেঞ্জ যেমন শুষ্ক অঞ্চলে উপকূল ক্ষয় ও পরিবেশবান্ধবভাবে লবণ সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে চান বিজ্ঞানীরা।