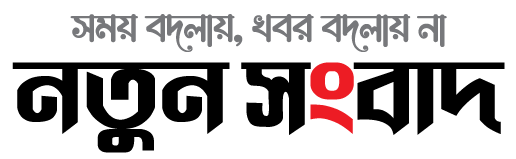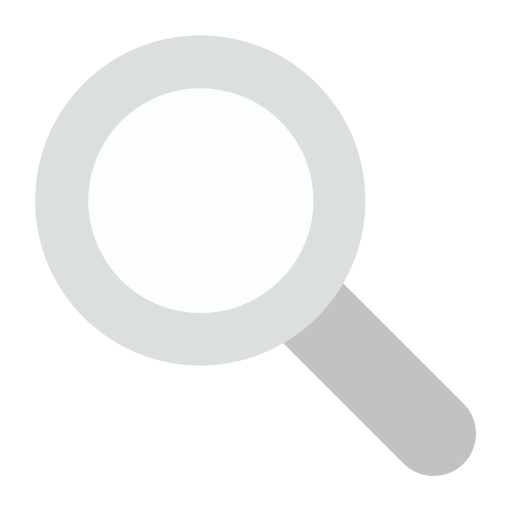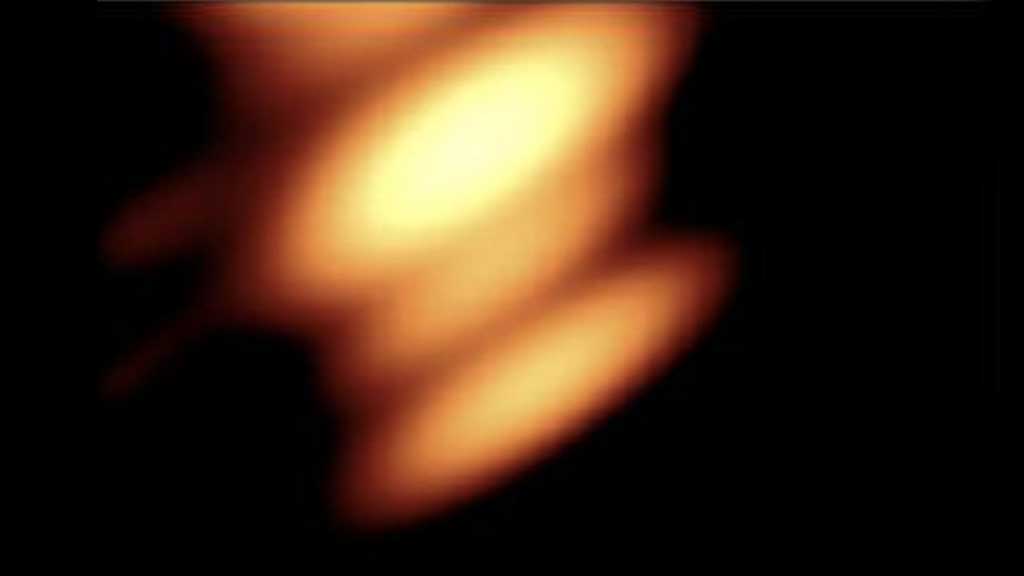এ দুটি ব্ল্যাক হোল রয়েছে ‘ওজে২৮৭’ নামের এক কোয়াসারের মধ্যে, যা পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ‘ক্যান্সার’ তারাগুচ্ছে অবস্থিত।
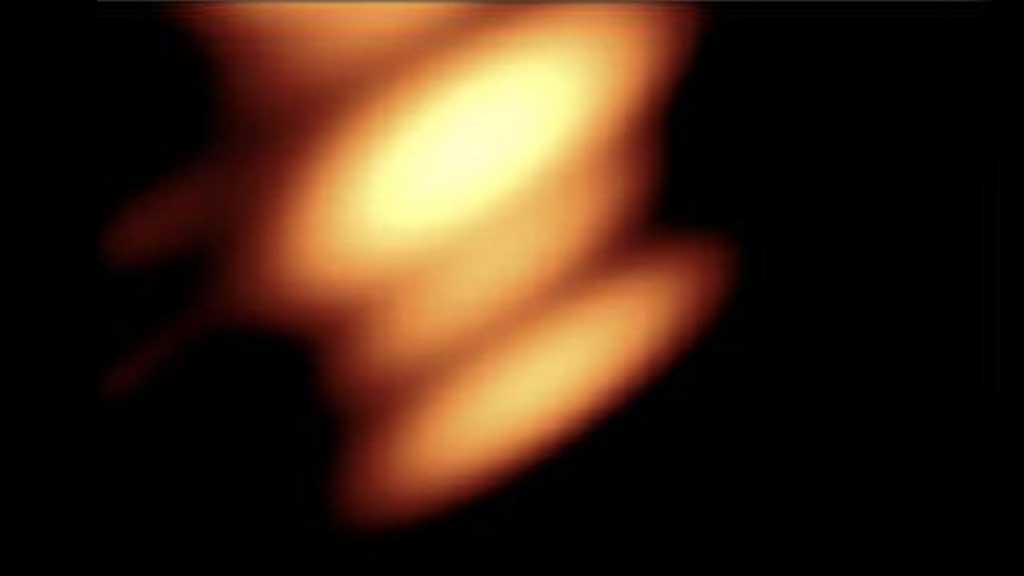
সংগৃহিত
কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, মহাবিশ্বের অন্যতম উজ্জ্বলতম বস্তু কোয়াসাসের ভেতরে একটির বদলে দুটি ব্ল্যাক হোল থাকতে পারে, যেখানে ব্ল্যাক হোল দুটি একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, যেন এক ‘মহাকর্ষীয় নাচে’ মেতে রয়েছে এরা।
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দুটি ব্লাক হোলের এমন দৃশ্যের সরাসরি রেডিও ছবি ধারণের দাবি করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, যা মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে প্রতিবেদনে লিখেছে প্রযুক্তি বিষয়ক সাইট স্ল্যাশগিয়ার।
পৃথিবী ও মহাকাশে থাকা একাধিক টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এক জোড়া অতিভারী ব্ল্যাক হোল শনাক্ত করেছেন গবেষকরা, যা একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এ দুটি ব্ল্যাক হোল রয়েছে ‘ওজে২৮৭’ নামের এক কোয়াসারের মধ্যে, যা পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ‘ক্যান্সার’ তারাগুচ্ছে অবস্থিত।
দুটি ব্ল্যাক হোল পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয়ে প্রতি ১২ বছরে একবার একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে। ব্ল্যাক হোলকে খালি চোখে দেখা না গেলেও এদের উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের বুঝতে পারার কারণ, এরা অত্যন্ত দ্রুতগতির কণার জেট মহাকাশে ছুড়ে দেয়, যা এদের অস্তিত্বেরই জানান দেয়।
এসব কণার জেটের মধ্যে একটি জেট আসে ছোট ব্ল্যাক হোল থেকে ও অন্যটি আসে এক হাজার আটশ কোটি সূর্য ভরের সমান ব্ল্যাক হোল থেকে, যা এই সিস্টেমের কেন্দ্রে অবস্থিত। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোলগুলোর প্রায় অর্ধেক আকারের এ ব্ল্যাক হোলটি।
এ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি প্রকাশ পেয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক জার্নাল ‘অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল’-এ।
গবেষণা প্রথমবারের মতো নিশ্চিত করেছে, দুটি ব্ল্যাক হোলের জোড়া সত্যিই থাকতে পারে– এমন ধারণা আগে কেবল মহাকর্ষ তত্ত্ব ও পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই ভাবা হত।
এ বিস্ময়কর আবিষ্কারটি সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর রেডিও টেলিস্কোপ ও মহাকাশে থাকা বিভিন্ন স্যাটেলাইটের তথ্য একত্র করে। এ গবেষণায় মূল ভূমিকা রেখেছে রাশিয়ার ‘রেডিওঅ্যাস্ট্রন’ নামের স্যাটলাইট, যার কক্ষপথ চাঁদের দূরত্বের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে সাধারণ অপটিক্যাল টেলিস্কোপে দেখা ছবির চেয়ে প্রায় এক লাখ গুণ বেশি স্পষ্ট ছবির দেখা পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা!
দুটি ব্ল্যাক হোল কি সত্যিই একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে?– এ ছবিই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, যা বহু বছর ধরে জানতে চাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা।
ব্ল্যাক হোল নিয়ে গবেষণা শুরুই হয়নি, এমনকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘কোয়াসার ওজে২৮৭’। ১৯শ শতাব্দীতেই প্রথম এই কোয়াসারের ছবি তুলেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তবে ওই সময় তারা বুঝতেও পারেননি এটি আসলে কী।
এরপর ১৯৮২ সালে ফিনল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আইমো সিলানপা কিছু অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘কোয়াসার ওজে২৮৭’-এর উজ্জ্বলতা প্রতি ১২ বছর পরপর নিয়মিতভাবে বাড়ে ও কমে।
এ রহস্যময় নিয়মিত পরিবর্তন থেকেই ধারণা মেলে, কোয়াসারটির ভেতরে আসলে দুটি ব্ল্যাক হোল একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। যখন ছোট ব্ল্যাক হোলটি বড় ব্ল্যাক হোলের আশপাশের গরম গ্যাস ও ধূলোর বলয় ভেদ করে যায় তখনই প্রচণ্ড আলো বা উজ্জ্বলতার বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে সেই ১২ বছরের আলোচক্রের পুনরাবৃত্তির দেখা মেলে।
বহু দশক ধরে গবেষকরা এই তত্ত্বটি প্রমাণ করতে পারেননি, কারণ তাদের কাছে সেই সময় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ছিল না। নাসার ‘টেস’ স্যাটেলাইটের মতো বিভিন্ন যন্ত্র তারার আলোতে ওঠানামা নিশ্চিত করতে পারলেও এসব টেলিস্কোপের সক্ষমতা কখনোই এত সূক্ষ্ম ছিল না যে, এরা আসলে সেই ব্লাক হোল জোড়াটিকে আলাদা করে দেখতে পারে।
তবে পরিস্থিতি বদলায় যখন ফিনল্যান্ডের ‘ইউনিভার্সিটি অফ টার্কু’র গবেষক মৌরি ভাল্টোনেনের নেতৃত্বে ‘ওজে২৮৭’-এর ছায়াপথে উন্নত রেডিও ইন্টারফেরোমেট্রি প্রযুক্তি প্রয়োগ করেন। তারা যে ছবি পান তা আগে গণনা করা মডেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। ফলে সঠিকভাবে সেই দুটি ব্লাক হোলের অবস্থান নির্ধারণ করতে পেরেছেন গবেষকরা।
‘ইউনিভার্সিটি অফ টার্কু’র প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ভ্যালটোনেন বলেছেন, এসব ব্লাক হোল সম্পূর্ণ অন্ধকার ও সরাসরি দেখা বা শনাক্ত করা যায় না। তবে এদের আশপাশে ঘূর্ণায়মান জ্বলজ্বলে গ্যাস ও কণার প্রবাহ এদের উপস্থিতিরই ইঙ্গিত দেয়।
এসব প্রমাণ যতই আশাব্যঞ্জক হোক না কেন দৃশ্যমান প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এখনই কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছেন না ‘ইউনিভার্সিটি অফ টার্কু’র গবেষকরা।
তারা বলছেন, আসলেই সেখানে দুটি ব্লাক হোল রয়েছে কি না, নাকি একই ব্লাক হোল থেকে বের হওয়া দুটি গ্যাস প্রবাহ কেবল একে অপরের ওপর পড়ে রয়েছে তা নিশ্চিত করতে আরও এক উচ্চ-রেজুলিউশনের ছবি প্রয়োজন। বিষয়টি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, গোপনে থাকা বিশালাকার ব্লাক হোলকে খুঁজে বের করা কতটা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ।